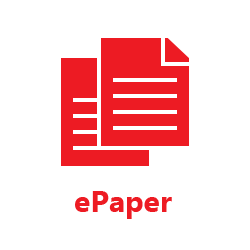সাইবার অপরাধ দমন ও অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিতে নতুন অধ্যাদেশ জারি করেছে সরকার। তবে সমালোচিত ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩’ বাতিল করে ‘সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ আইনি কাঠামো চালু হলেও রয়ে গেছে পুরোনো বিতর্কিত ধারা। এর মধ্যে অন্যতম পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান।
অধ্যাদেশ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নতুন অধ্যাদেশের ৩৫ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে, যদি পুলিশ মনে করে কোনো ব্যক্তি এ আইনের অধীনে অপরাধে লিপ্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাহলে তাকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করা যাবে। আগের আইনেও এ বিতর্কিত ক্ষমতা ছিল, যেটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকারকর্মী ও নাগরিক সমাজ উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল।
তবে এক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনও এসেছে। নতুন অধ্যাদেশে আর নেই মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা নিয়ে সমালোচনার অপরাধের দণ্ডবিধান। পূর্ববর্তী আইনের ২১ ধারায় এসব বিষয়ে ‘বিদ্বেষ’ ছড়ানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। এবার সেই ধারা পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
অন্যদিকে নতুন অধ্যাদেশে সাইবার অপরাধের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুল ব্যবহার করে কোনো নেটওয়ার্কে অবৈধ প্রবেশ বা ক্ষতিসাধনকে এখন থেকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। ১৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোয় এআই দিয়ে হামলা চালালে, তার সর্বোচ্চ ৫ বছরের জেল এবং ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
অধ্যাদেশে আরও উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো অনলাইন জুয়া নিষিদ্ধ করা। ২০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি জুয়ার অ্যাপস তৈরি, পরিচালনা বা প্রচার করেন, অথবা খেলায় অংশগ্রহণ করেন, তাহলে সেটি হবে অপরাধ। এর সর্বোচ্চ শাস্তি ২ বছরের কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ড।
তবে প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ দমনকে কেন্দ্র করে যে নতুন সংজ্ঞা ও শাস্তির বিধান যুক্ত করা হয়েছে, তা যেমন প্রশংসিত হচ্ছে, তেমনি কিছু ধারা নিয়ে নতুন উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে আইনটির সংজ্ঞায় (২-এর ল) বলা হয়েছে, ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে ‘সাইবার সুরক্ষা’ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ব্যক্তির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুলের অ্যাকসেসকেও এ সুরক্ষার আওতায় ধরা হবে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এতে কি সরকারের নজরদারি ক্ষমতা আরও বাড়ছে?
অন্যদিকে ৫০ (৪) ধারায় বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী আইন অনুযায়ী বিচারাধীন ও তদন্তাধীন থাকা ৯টি ধারার সব মামলা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি আদালতের দেওয়া সাজাও কার্যকর হবে না। অর্থাৎ আগের আইনের অধীনে দায়ের হওয়া হাজারো মামলার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। যারা এ আইন দিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, তারা কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রযুক্তিবিদ ফাহিম মাশরুর যুগান্তরকে বলেন, ‘আমরা সব সময়ই এ ধরনের প্রস্তাবনার বিরোধিতা করে এসেছি। আমাদের যেই ড্রাফটটি দেখানো হয়েছিল, তাতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন হঠাৎ করে এটি অন্তর্ভুক্ত হলো কীভাবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে জরুরি, তবে সেটা যেন নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন না করে। পুলিশের বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করার ক্ষমতা বহাল রাখা বাস্তবে আইনের অপব্যবহারকে উৎসাহ দিতে পারে, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাম্য নয়।’
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নতুন অধ্যাদেশে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি আছে। যেমন: অপব্যবহারের সুযোগ কমানো ও বিতর্কিত ধারার অপসারণ। তবে ‘বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার’, নজরদারি ও জবাবদিহিহীনতার আশঙ্কা এখনো থেকেই যাচ্ছে। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঝুঁকি স্পষ্ট। জবাবদিহির বাইরে থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহারও হতে পারে। এজেন্সি ও পুলিশের হাতে এত ক্ষমতা মানেই সরকারের ইচ্ছামতো আইন প্রয়োগের আশঙ্কা।
এছাড়া ২৫ সদস্যের সাইবার কাউন্সিলে মাত্র দুজন আইসিটি বা মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তাও সরকার মনোনীত, যে কারণে সরকারের বাইরে অংশীজনের বাস্তব প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকবে ন।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, পুলিশের বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা একেবারেই সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে, বিধানটা আগের মতো উন্মুক্ত নয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে এটি কেবল ‘ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিআইআই) এবং এসব কৌশলগত অবকাঠামোয় সাইবার হামলার মতো উচ্চঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ ধরনের অবকাঠামো মাত্র ৩৫টি। উদ্দেশ্য একটাই-কৌশলগত এবং অর্থনৈতিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এসব অবকাঠামো সুরক্ষায় দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সক্ষমতা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে যখন আদালত অবকাশে থাকে। পাশাপাশি গ্রেফতার বা জব্দের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আদালতে হাজির করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে, যা আইন প্রয়োগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।